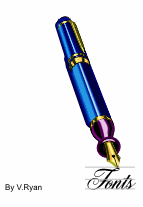
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী
(সংকেত: আদিবাসী এবং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী; বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর পরিসংখ্যান; চাকমা; মারমা; তঞ্চঙ্গ্যা; গারো; রাখাইন; মনিপুরী; হাজং; সাঁওতাল; খাসিয়া; অন্যান্য; বর্তমানে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের অবস্থা; উপসংহার।)
বাংলাদেশ একটি বহু জাতি, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং ভাষার দেশ। এদেশের বাংলা ভাষাভাষি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালিদের পাশাপাশি সুদীর্ঘকাল ধরে বসবাস করছে বেশ কিছু ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়। আচারে, অনুষ্ঠানে, ধর্মে, ভাষায়, সংস্কার-সংস্কৃতিতে এরা বাঙালিদের থেকে স্বতন্ত্র। এরা বাংলাদেশেরই অবিচ্ছেদ্য এবং অনিবার্য অংশ।
আদিবাসী এবং ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীঃ আদিবাসী এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Aborigines, শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Aborigine থেকে এসেছে যার অর্থ “শুরু থেকে” অর্থাৎ কোনো দেশে বসবাসরত আদিম জনগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলা হয়। অন্যদিকে, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী বলতে মূলত প্রধান জাতির পাশাপাশি বসবাসরত সংখ্যালগিষ্ঠ এবং অপেক্ষোকৃত অনগ্রসর জাতি বা সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়।
বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানঃ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে ২৯টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যাদের বেশিরভাগই পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন পাহাড়ি এলাকায় বাস করে। ২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেখা গেছে বাংলাদেশে মোট আদিবাসীদের সংখ্যা ৩ লাখ ৬৪ হাজার ৭৭৫ জন। তবে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের দেওয়া তথ্যানুযায়ী ৪৫টি ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে এবং সর্বমোট ২০ লক্ষাধিক আদিবাসী আছে বলে জানা যায়। বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- চাকমা, মারমা, রাখাইন, তঞ্চঙ্গ্যা, মনিপুরি, গারো, হাজং, সাঁওতাল, খাসিয়া প্রভৃতি নৃ-গোষ্ঠীগুলো। এরা বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, সিলেট, রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার প্রভৃতি অঞ্চলগুলোতে যুগ যুগ ধরে বাস করছে।
চাকমাঃ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ সম্প্রদায় হলো ‘চাকমা’। চাকমারা নিজেদেরকে বলে চাঙমা। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষত রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন প্রভৃতি জেলায় এদের বাস। এরা আবার ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এদের নিজস্ব সামাজিক, প্রশাসনিক ও বিচার ব্যবস্থা আছে যার প্রধান দায়িত্বে আছে রাজা। রাজাই চাকমাদের প্রথা, রীতি-নীতি নির্ধারণ, ভুমি, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা, গ্রামের কোন্দল এবং নানা সমস্যার নিষ্পত্তি করে। চাকমাদের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। ফলে পুত্রসন্তানরাই কেবল পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। কৃষি এদের প্রধান জীবিকা হলেও বর্তমানে চাকমারা চাকুরী ও ব্যবসাক্ষেত্রেও জায়গা করে নিয়েছে। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে চাকমাদের স্বাক্ষরতার হার (৩৭.৭%) সবচেয়ে বেশি। এরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলোর মধ্যে আছে মাঘী পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান, মধু পূর্ণিমা, ফানুস ওড়ানো প্রভৃতি। চাকমাদের অন্যতম বড় উৎসব হলো বিজু উৎসব।
মারমাঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহৎ সম্প্রদায় হলো ‘মারমা’। পার্বত্য জেলাগুলোতে মারমাদের বসবাস দেখা গেলেও এরা মূলত বান্দরবনের অধিবাসী। মায়ানমার থেকে এসেছে বলে এদেরকে মারমা বলা হয়। তবে মারমা শব্দটি এসেছে ‘ম্রাইমা’ শব্দ থেকে। বান্দরবনে প্রায় ১ লাখ মারমা বাস করে। চাকমাদের মতো এদেরও সামজিক বিচার-আচারের দায়িত্ব রাজার হাতে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা হলেও মারমা মেয়েরা পৈতৃক সম্পত্তির সমান উত্তরাধিকার লাভ করে। জুম চাষ, নদীর মাছ ও কাঁকড়া শিকার এবং কাপড়, চুরুট প্রভৃতি তৈরি করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রসর হয়ে এরা চাকুরী, ব্যবসাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করছে। মারমারা নিজস্ব ভাষায় কথা বললেও লেখার ক্ষেত্রে বর্মিজ বর্ণমালা ব্যবহার করে। মারমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবের মধ্যে আছে বৌদ্ধ পূর্ণিমা, কঠিন চীবর দান, ওয়াগ্যোয়াই প্রভৃতি।
তঞ্চঙ্গ্যাঃ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীর মধ্যে তঞ্চঙ্গ্যা উল্লেখযোগ্য। রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় এদের বাস। তঞ্চঙ্গ্যারা নিজেদের স্বতন্ত্র্য জাতি বলে দাবি করলেও নৃতাত্ত্বিকগণ মনে করেন এরা চাকমা জাতির একটি উপগোত্র। সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রথা, রীতি-নীতির দিক থেকে চাকমাদের সাথে এদের যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষা ইন্দো-এরিয়ান ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তঞ্চঙ্গ্যারা একে ‘মনভাষা’ বলে উল্লেখ করে।
গারোঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মধুপুরের গভীর অরণ্য, অরণ্য সংলগ্ন এলাকা এবং গারো পাহাড়ের টিলায় বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী গারোদের বাস। এছাড়া নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল ও সুনামগঞ্জ অঞ্চলে কিছু কিছু গারোদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। নৃতান্ত্রিকগণ মনে করেন এরা মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর একটি শাখা। গারোরা নিজেদের আচ্ছিক মান্দি অর্থাৎ পাহাড়ের মানুষ বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করে। তবে যারা সমতলে বাস করে তারা কেবল মান্দি বলে পরিচয় দেয়। গারোদের সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক। গারোদের ভাষার নাম আচ্ছিক ভাষা। তবে সমতলে বসবাসকারী গারোদের ভাষা আলাদা, তাদের ভাষার নাম মান্দি ভাষা। গারোরা স্বতন্ত্র ধর্মমতে বিশ্বাসী আর তাদের সাংস্কৃতিক উৎসব, আচার-অনুষ্ঠানের মূলে রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস। গারোদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব হলো নবান্ন বা ওয়ানগালা উৎসব।
রাখাইনঃ রাখাইন সম্প্রদায় মূলত মায়ানমারের একটি জাতিগোষ্ঠী। পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু অংশ, রাঙ্গামাটি ও বান্দবান জেলায় রাখাইনদের বাস। রাখাইনরা সাধারণত মগ নামে পরিচিত। রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী। ফলে এদের প্রধান উৎসবগুলো হলো- বুদ্ধের জন্মবার্ষিকী পালন, বৈশাখী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা প্রভৃতি। এছাড়া রাখাইনরা সংক্রান্তিতে ৩ দিনব্যাপী সাংগ্রাই উৎসব পালন করে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে। পুরুষেরা লুঙ্গি, ফতুয়া আর নারীরা লুঙ্গি, ব্লাউজ, অলংকার এবং মাথায় ফুল পরিধান করতে পছন্দ করে। রাখাইনদের বিয়েতে পুরুষদের পণ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে।
মনিপুরীঃ মনিপুরীদের আদি নিবাস ভারতের মনিপুর রাজ্যে। বার্মা-মনিপুর যুদ্ধের সময় এরা এসে বৃহত্তর সিলেটে আশ্রয় নিয়েছিল। এছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং ময়মনসিংহেও মনিপুরীদের দেখতে পাওয়া যায়। ভাষাগত ও ধর্মীয় ভিন্নতার ফলে মনিপুরী সম্প্রদায় আলাদা আলাদা তিনটি উপ-গোষ্ঠীতে বিভক্ত। (১) বিষ্ণুপ্রিয়া, (২) মৈতৈ, (৩) পাঙন। ২০০৩ সালের এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৪০ হাজার বিষ্ণুপ্রিয়া মনিপুরী এবং ১৫ হাজার মৈতৈ মনিপুরী আছে। মনিপুরীদের সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও ঐতিহ্যাবাহী। বিশেষ করে মনিপুরী নৃত্য আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত। মনিপুরীদের সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান হচ্ছে রাসপূর্ণিমা।
হাজংঃ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাজং সম্প্রদায়ের দেখা মেলে নেত্রকোনা জেলায়। হা মানে মাটি আর জং অর্থাৎ পোকা। প্রকৃতপক্ষে কৃষিকাজের সাথে সখ্যতার কারণে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে হাজং। বাংলাদেশে প্রায় ৩০০০ হাজং এর বাস। হাজং বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন প্রভৃতি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার মাধ্যমে এরা ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। হাজংদের নিজস্ব ভাষা আছে। হাজংদের সবচেয়ে বড় উৎসব ‘প্যাক খেলা’ উৎসব। এদের কিছু অংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং কিছু অংশ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। ভাত, মাছ, সবজি ছাড়াও কচি বাঁশের গুড়া বা মিউয়া এদের প্রিয় খাবার।
সাঁওতালঃ পূর্বভারত ও বাংলাদেশের বৃহত্তম আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি হলো সাঁওতাল। বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে বিশেষত দিনাজপুর এবং রংপুরে সাঁওতালদের বাস। সাঁওতাল সম্প্রদায় আবার ১২টি উপগোত্রে বিভক্ত। এরা মাটির তৈরি ছোট ছোট ঘরে বাস করে। সাঁওতালদের প্রধান পেশা কৃষি। সাঁওতালদের প্রধান দেবতা বোংগা। এরা মূলত সূর্যের পূজা করে। সাঁওতালদের বার্ষিক উৎসবের নাম সোহরাই। এ উৎসবে সাঁওতাল মেয়েরা দলবেঁধে নাচে। সাঁওতালদের প্রধান খাদ্য ভাত। এছাড়া মাছ, কাঁকড়া, শুকর, মুরগি, খরগোস, গুইসাপ, ইঁদুর এবং বেজির মাংস খেতে পছন্দ করে সাঁওতালরা। সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণে ইতিহাসে এরা বিশেষ স্থান দখল করে আছে।
খাসিয়াঃ বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে খাসিয়াদের বাস। মূলত ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন গভীর অরণ্যে থাকতেই পছন্দ করে এরা। বাংলাদেশে বসবাসকারী খাসিয়ারা সিনতেং গোত্রভুক্ত। খাসিয়ারা মূলত কৃষিজীবী। গভীর অরণ্যে এরা পান চাষ করে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার কারণে নারীরা বিয়ে করে বর নিয়ে আসে নিজের বাড়িতে। সম্পত্তির মালিকানাও নারীরাই লাভ করে।
অন্যান্যঃ আলোচিত সম্প্রদায়গুলো ছাড়াও বাংলাদেশে ত্রিপুরা, খিয়াং, মুন্ডা, চক, লুসাই প্রভৃতি আরো কিছু কিছু ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী বসবাস করে থাকে।
বর্তমানে ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের অবস্থাঃ অতীতে যদিও এই ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে নানাভাবে নির্যাতিত, নিগৃহীত হতো কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে সরকার ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠীদের জন্য বিশেষ কোটা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা সহায়তাসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে প্রাগসর করে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো এখন কেবল কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করে না বরং তারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সম্মানজনক পদে চাকুরী করছে। এছাড়া ব্যবসা, রাজনীতি, শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসার লক্ষ্যে তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
উপসংহারঃ বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়গুলো এ দেশের নাগরিক। তাই তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। বর্তমানে কিছু কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলে আরো ব্যাপক পরিসরে তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, রীতি-নীতি, জীবনযাপন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে গবেষণা হওয়া প্রয়োজন এবং এগুলো সংরক্ষণ করার যথাযথ ও কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া উচিত।